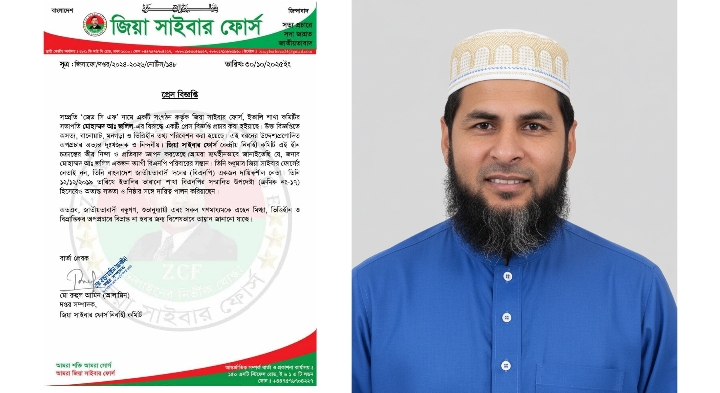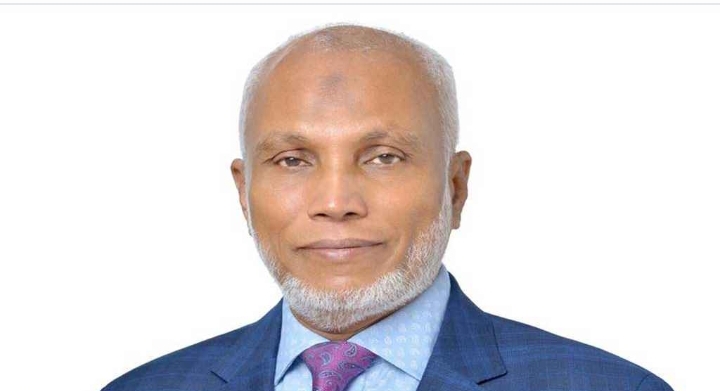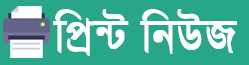
◻️ জসিম উদ্দীন মাহমুদ তালুকদার, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশের বেড়িবাঁধ ও নদ-নদীগুলো একসময় আশীর্বাদ হলেও কালক্রমে তা যেন বিভিন্ন এলাকার মানুষের জন্য আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে পানিশূন্যতা, বর্ষায় প্রচন্ড ভাঙনের মুখে পড়ছে উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দারা।
বন্যা নিয়ন্ত্রণকারী বাঁধ ও নদীভাঙনে গ্রামের পর গ্রাম, জনপদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদি বিলীন হয়ে দেশ ও জনসাধারণ অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হলেও তা রোধে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। বছরের পর বছর ধরে ভাঙনে মানুষ সর্বহারা হলেও এর কোনো স্থায়ী প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না।
‘আমার চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়, তখুনি আমার ভয়।/মনে হয় চোখ যেন আস্তে আস্তে কানের দিকে সরে যাচ্ছে।/কিম্বা শ্রবণেন্দ্রীয় এসে আমার চোখের ভেতর/শব্দের রাজদণ্ড ধরেছে।/যেদিকে তাকাই, শুধু শুনতে পাই। শুনতে পাই/দূরাগত ভাঙনের শব্দ।/…যেদিন নদী এসে আমাদের বাড়িটাকে ধরলো/সেদিনের কথা আমার চোখের ওপর স্থির হয়ে আছে।/বাক্সপেটরা থালা ঘটিবাটি নিয়ে আমরা/গাঁয়ের পেছনে বাপের কবরে গিয়ে দাঁড়ালাম।/…তারপর ভাঙনের রেখা পেছনে রেখে/আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছিড়ে পড়লাম।/কেউ গেলাম মামুর বাড়িতে। কেউ ফুপুর।… (সংক্ষেপিত, চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়, কবি আল মাহমুদ)
কবি আল মাহমুদের কবিতার চিত্রই আমাদের নদীভাঙন অনেক এলাকার চিত্র। বাংলাদেশ একটি পলি গঠিত বদ্বীপ। এই দ্বীপে ভাঙা-গড়ার খেলা চলছে হাজার হাজার বছর ধরে। গত চার দশকে বাংলাদেশ একটি আস্ত জেলার চেয়েও বেশি ভূমি নদীতে হারিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা ‘সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস’-এর (সিইজিআইএস) তথ্য মতে, প্রতি বছর ভাঙনে নদীতে চলে যায় প্রায় ৪ হাজার হেক্টর জমি। আর এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লাখ খানেক পরিবার। সব কিছু হারিয়ে নানা ধরনের দুর্দশার মুখোমুখি হয় তারা।
‘নদীর ধারে বাস তো ভাবনা বারো মাস’- দেশে এ রকম একটি কথা প্রচলিত আছে। চট্টগ্রাম, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাটসহ এলাকার মানুষের কাছে শুনি অনেকের করুণ পরিণতি। বাংলাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে ২৫৪টি নদী আছে। এর মধ্যে প্রধান নদীগুলো হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র, সবচেয়ে বেশি ভাঙনের শিকার হচ্ছে। দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভাঙনপ্রবণ নদী যমুনা। এছাড়া তিস্তা, ধরলা, আত্রাই, কুশিয়ারা, খোয়াই, সুরমা, চট্টগ্রাম সাঙ্গু, কর্ণফুলী, গোমতী, মাতামুহুরী, মধুমতী ইত্যাদি নদীভাঙন প্রবণ। নদী ভাঙন এ দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে যেকোনো দুর্যোগের চেয়ে বেশি মাত্রায় ধ্বংস করছে। নদীভাঙনকে অনেকে বলে থাকেন Slow and Silent killer-Disaster । কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা, লেখালেখি বা চিন্তাভাবনা খুব কম।
বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ‘উন্নয়ন অন্বেষণে’র এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে শিকার হচ্ছে প্রায় ১০ লাখ মানুষ। এদের আবার বেশির ভাগই পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে শহর অভিমুখে ছুটছে। সত্তর ও আশির দশক থেকে এদেশে নদীভাঙনের তীব্রতা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ক্ষয়ক্ষতি। প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে ৮ হাজার ৭০০ হেক্টর জমি নদীতে বিলীন হয়। যার বেশিরভাগ কৃষিজমি। ক্ষতিগ্রস্ত অর্ধেক লোকেরই টাকার অভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা সম্ভব হয় না। তারা হয় গৃহহীন, ছিন্নমূল। এরা সাধারণত বাঁধ, রাস্তা, পরিত্যক্ত রেলসড়ক, খাস চর, খাস জমিতে অবস্থান নেয়। অনেকেই আবার কাজের খোঁজে আসে শহরে। নদীভাঙনের কারণে বেড়ে যাচ্ছে সামাজিক ও পারিবারিক সংকট, বাড়ছে বেকারত্ব। ‘উন্নয়ন অন্বেষণে’র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ভূমিহীনদের ৫০ শতাংশই নদীভাঙনের শিকার। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, নদীভাঙনের কারণে এক ব্যক্তির জীবনে গড়ে ২২ বার ঠিকানা বদল করতে হয়।
নদীভাঙনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী যা সমাজ জীবনের ওপর প্রভাব পড়ছে। এর ফলে গতকালের আমির আজ ফকির ও আশ্রয়হীন হয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অভাবের তাড়নায় কিংবা অন্যের চাপের মুখে অবশিষ্ট জমিজমা, গবাদিপশু এবং মূল্যবান সামগ্রী হাতছাড়া করে ফেলে। অনেক পরিবার অতিমাত্রায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে পতিত হচ্ছে। খাবার পানি ও পয়ঃপরিচ্ছন্নতার তীব্র সংকট দেখা দেয়। নারীদের ব্যক্তিগত বা দৈহিক নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয় এবং নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। বহুসংখ্যক লোক কর্মসংস্থান লাভের বা বেঁচে থাকার আশায় এলাকা ত্যাগ করে শহর বা অন্য কোনো স্থানে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়ে চলে যায়। অনেকে বস্তিতে বসাবাস করছে। বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের মাঝে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছে। অনেক স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। অনেকের বাস্তুচ্যুত হওয়ার কারণে পড়াশোনার বিঘœ হয় বা অনেকের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। শত শত বা হাজার হাজার মানুষ বাঁধ বা শহরের বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিশুরা বাঁধ বা বস্তির জীবনে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে পুষ্টিহীনতার প্রসার ঘটায়। শিশুশ্রম ও শিশু নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের সামাজিক অবস্থানের চরম অবনতি ঘটে। বিবাহ বিচ্ছেদ, স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক পরিবার পরিজন ত্যাগ, বহু বিবাহ ইত্যাদি নেতিবাচক ঘটনা বৃদ্ধি পায়। পরিবারের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক স¤পর্ক ও সহমর্মিতা শিথিল হয়ে পড়ে। নদীতে ভেঙে যাওয়া জমি জেগে উঠলে তা দখলের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়, কোন্দল-মামলা বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে রক্তপাত হয়। সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িয়ে পরে অনেকে।
বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই প্রধান তিনটি নদ-নদী অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রধান তিন নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী, ছাড়াও নদীবিধৌত বাংলাদেশের ছোটবড় নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ৩০০টি। এসব নদ-নদীর তটরেখার দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় ২৪ হাজার ১৪ কিলোমিটার। এর মধ্যে কমপক্ষে প্রায় ১২ হাজার কিলোমিটার তটরেখা নদীভাঙন প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশজুড়ে থাকা কয়েকশত নদী-উপনদীতে ভাঙন হলেও সবচেয়ে বেশি ভাঙনপ্রবণ যমুনা, পদ্মা ও মেঘনা। স্বাধীনতার পর থেকে নদীভাঙনে এ দেশের পৌনে ২ লাখ হেক্টরের মতো জমি বিলীন হয়েছে বলে বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে এসেছে। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমেই সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙনে লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ‘সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস’-এর তথ্য মতে, এই এক নদীর ভাঙনেই ৯০ হাজার হেক্টরের মতো জমি হারিয়ে গেছে। পদ্মা বা যমুনা নদীর ভাঙনও প্রবল। প্রতি বছর গ্রামের পর গ্রাম পানিতে তলিয়ে যায়। নদীভাঙনে মানুষের ভিটেমাটির সঙ্গে এলাকার স্কুল-কলেজ, হাসপাতালসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও হারিয়ে যায়। নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাথমিক সহায়তায় এগিয়ে আসে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা। কিন্তু কিছুদিন পরে এসব অসহায় মানুষকে নিজের পথ বেছে নিতে হয়।
পলিমাটি গঠনের জন্য বাংলাদেশের নদীভাঙনের কারণ। বর্ষাকালে নদীর প্রবাহের বিস্তৃতি অনেক বেশি থাকে। বর্ষা শেষে নদীর স্রোত ও পরিধি অনেক কমে যায়। এতে দুই কূলে ভাঙন হয়। অনেক স্থানে নদীর দুই কূলে স্থাপনা থাকে। এতে নদীর গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নদীপাড়ে শক্তভাবে পাড় দেওয়া হয় না। নদীপথ শেষের দিকে স্রোতের বেগ কম থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে নদীর দুই কূল স্রোতের জলে নরম হয়ে যায়। পরে সেখানে ভাঙন সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নদী শাসন বা সরকারি-বেসরকারি বরাদ্দ যথাযথ ব্যবহার হয় না। তাই নদী শাসন কাজে ফাকফোঁকর থেকে যায়।
এ দেশে নদীভাঙন একটি অতি প্রাচীন ও ভয়াবহ সমস্যা। পুরো বর্ষাকালজুড়েই চলতে থাকে ভাঙনের তান্ডবলীলা। বর্ষা শেষে ভাঙনের প্রকোপ কিছুটা কমলেও বছরজুড়ে তা কমবেশি মাত্রায় চলতে থাকে। প্রাকৃতিক খেলা আমাদের পক্ষে বন্ধ করা কঠিন। কিন্তু আমরা, মানুষরা, যেসব কারণ সৃষ্টি করেছি, সেগুলো যদি রোধ করা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে নদীভাঙনের ক্ষতি রোধ সম্ভব হবে। নদীর পাড়ের ঘাস, ঝোপঝাড়, কাশবনসহ অন্যান্য বন উজাড় করে ফেললে মাটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পানির তোড়ে ভাঙন সৃষ্টি হয়। এছাড়া অপরিকল্পিতভাবে নদী খনন বা ড্রেজিংয়ের কারণে ক্ষতির শিকার হয় নদী। বাংলাদেশে নদীভাঙন প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় এর পূর্বাভাস এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া গেলে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যাবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
নদীভাঙন এলাকায় সরকারের নজর আছে। তবে আরো বরাদ্দ বেশি দেওয়া যেতে পারে। বিদেশি অনেক সাহায্য সংস্থা অপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। দেশি অনেক সংস্থাও এ রকম করে। সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় মাস্টারপ্লানের মাধ্যমে নদীভাঙন ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এতে সুষ্ঠু-বণ্টন হতে সহয়তা করবে। নদীতে চর জেগে উঠলে ভাঙনের শিকার-ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সুষম বণ্টন করা দরকার। এ ব্যাপারে প্রশাসন কঠোরতা অবলম্বন করতে পারে। ছোট আকারের নদীগুলোর ভাঙন ঠেকাতে কর্তৃপক্ষ কিছুটা সক্ষম হলেও প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি বরাদ্দের অভাবে বড় নদীর ক্ষেত্রে উদ্যোগগুলো তেমন সফল হচ্ছে না। এ ব্যাপারে আমরা সমন্বিত পরিকল্পনা করে স্বল্প বরাদ্দ সদ্ব্যবহার করতে পারি। দু-একটা করে পর্যায়ক্রমে বড় প্রকল্প গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে পারি।